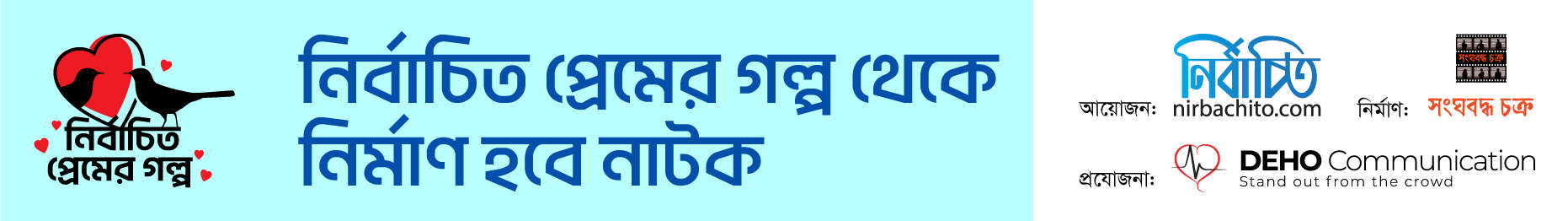রান্না-বান্না, নাওয়া-খাওয়াসহ ঘর-গৃহস্থালির নানা কাজে শান্ত দিঘির জল যথেচ্ছা ব্যবহার করার পরও দিঘি যেমন বিশেষ কোনো গুরুত্ব বা ধন্যবাদ পায় না পাড়ার লোকের কাছে, আব্বাও আমাদের কাছে অনেকটা সেরকম। তিনি আমাদের অথৈ জলের দিঘি। সেই দিঘির জলে আমরা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বেড়াই, কলহাস্যে-কলকাকলিতে সাড়া ফেলে দিই পাড়াময়, সেই জলেই রসুইঘরে পাতা আলোক চুলাতে শুকনো বাঁশ পাতার লাকড়িতে ফুটে চাল হয় ভাত, ঝিঙে-সজনের তরকারিতে ঝোলের বলক ওঠে, কাঞ্চনবিঘার মাঠে ভরদিন চড়ে বেড়িয়ে দিনান্তে ঘরে ফেরা তৃষ্ণার্ত গবাদিপশুগুলোর মুখের সামনেও ধরা হয় সেই জল, সন্ধ্যায় হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসার আগে মাটির সরাই কলসি ভরে রাখা সেই জলেরই এক গ্লাস পান করে তেষ্টা মেটাই আমরা। আমাদের সকল চাওয়া, সকল দাবি-দাওয়া, সখ-আহ্লাদ, সাধ-আকাঙ্ক্ষার শেষ গন্তব্য তিনি।
আব্বাকে আমরা ভাবতাম গাছ; টাকার গাছ! সে গাছে সব সময় পাড়ার মতো ফল থাকতো না বটে, বলা চলে অধিকাংশ সিজনে নিষ্ফলাই থেকে যেতো সে গাছ। মাসের পর মাস বেতন হতো না, বাঁধা মুদি দোকানী মাফ চাই বলে হাত জোর করতো, মার সখ করে পালা মুরগির ডিমগুলো আমাদের পাতে না উঠে পাড়ার দোকানে দিয়ে বিনিময়ে আনা হতো নুন-তেল-এটা-ওটা, তবুও খুব বেশি ঝাঁকাঝাঁকি করলে দুই চার টাকা খসে পড়তো বৈকি। দুই ঈদের দিন, পাড়ায় বৈশাখী মেলার দিন, স্কুলে স্বাধীনতার অনুষ্ঠানের দিন অথবা আকস্মিক পাড়াগ্রামে হাজির হওয়া সার্কাসের দল, গাজির গান বা নসিমনের পালার দিন আব্বার পকেট ঝাঁকিয়ে আদায় করে নেওয়া ওই দুই চার দশ টাকাই আমাদের কাছে ছিল তখন আকবর বাদশার ধন। বাদশা আকবর যেমন তার রাজভাণ্ডারের অশেষ ঐশ্বর্য দিয়ে যা খুশি তাই করতে পারতেন, ওই দুই চার দশ টাকা দিয়ে আমরাও করতে পারতাম যা খুশি তাই। মুড়ির মোয়া বা গুড়ের সন্দেশ, চালের ঝুরি বা নারকেলের মালাই, গুড়ের জিলাপি, চিনা বাদাম, হাওয়াই মিঠাই, পানিফল কী হতো না তাতে। চাই কী মেলার শেষ বেলায় ফেরার পথে মায়ের জন্য একটা রঙিন হাড়ি আনাও অসম্ভব ছিল না তখন।
মেলা বা অনুষ্ঠানের সময় যত এগিয়ে আসতো, আব্বা তত আভাস দিতেন, এবার যেন ওসব বায়না ঝক্কা না করি। এবার সময় সুবিধার না। ছ’মাসের বেতন আটকে আছে। সরকারি স্কুলের মাস্টারদের বেতন ঠিকঠাক হলেও বেসরকারিদের বেতনের খবর নেই। সরকারের ভাবনা শুধু সরকারিওয়ালাদের নিয়ে। শিক্ষা বিভাগের হর্তাকর্তাদের হয়তো ধারণা, সরকারি চাকুরে শিক্ষকদের পরিবারের লোকজনের পেটেই শুধু ক্ষুধা আছে, বেসরকারিদের ওসব নেই। বেসরকারি শিক্ষক বা তাদের পরিবার পরিজন সব হাওয়া খেয়ে বাঁচে। আগে যেমন বাঁচতো, এখনো তেমনই বাঁচে! কাজেই তাদের বেতন মাসের পর মাস আটকে রাখলে বিশেষ কোনো ক্ষতি নেই।
প্রতি মাসের শুরুতে আব্বার মলিন মুখ আমাদের নজর এড়াতো না। হাটের দিনে লেজে মাথায় দড়ি বাঁধা বাঁকানো ইলিশ আসা বন্ধ হয়ে যেতো! মাসের পর মাস গরম মশলার ঘ্রাণ ছড়াতো না রসুইঘর থেকে! বাজারের ব্যাগ বারান্দায় গোঁজা থাকতে থাকতে ছাতা পড়ে যেতো তার ভেতরে! তবুও মেলা বলে কথা! স্কুলের বাৎসরিক আয়োজন বলে কথা। দিঘির জল কমে গেলেও যেমন তাতে স্নান-গোসল বন্ধ করে না লোকে, আব্বার মলিন মুখও আমাদের আটকে রাখতে পারতো না। আমরা ঠিকই ঝাঁকাঝাঁকি শুরু করতাম কয়েকটা খুচরা টাকার জন্য। তারপর তা পেয়ে গেলে আমাদের আর পায় কে!
সবচেয়ে বেশি আব্বার খোঁজ করতাম তখন আমরা হাটের দিন। টানাটানির সেই সময়ে ‘হাটবার’ প্রায়ই মিস হয়ে গেলেও হাট থেকে ফেরা আব্বার জন্য আমাদের অপেক্ষা কখনো মিস হতো না। হাটের দিন বেলা বাড়তে থাকার সাথে সাথে মা’র কাছে গিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করতাম- ‘ও মা, আব্বা কি হাটে গেছে আজ? কখন যাবে? কখন আসবে? এখনো যায়নি কেন? এত বেলা হলো এখনো আসে না কেন?’ এরকম নানারকম প্রশ্নে মাকে জর্জরিত করে ফেলতাম। বেলা যত বাড়তো, ঘুরে ফিরে এসে আব্বার হাট ফিরতির খবর জানার পায়তারাও বাড়তো আমাদের। কারণ প্রতি হাটবারে আব্বার তরিতরকারি, নুন তেলের ব্যাগের ভেতর কাগজের ঠোঙা বা ছোট পলিথিনে মোড়া অল্পকিছু সরভাজা, গজা বা বউ ঝুমঝুমি পাউরুটি কিছু না কিছু আসতোই। মা’র বলে দেওয়া সদাই পাতির কোনো একটা হয়তো বাদ পড়তো কখনো কখনো, কিন্তু আমাদের জন্য এইসব কখনোই বাদ পড়তো না। সামান্য মিষ্টি, বারোভাজার জন্য হাটবারে তীর্থের কাকের মতো আব্বার পথ চেয়ে বসে থাকতাম আমরা।
আব্বাকে আমরা ভাবতাম যাদুকর। যাদুকর যেমন তার যাদুর ঝোলার ভেতর থেকে হরেক জিনিস বের করে উৎসুক দর্শকদের চোখে তাক লাগিয়ে দিতো, আব্বাও দিতেন আমাদের তেমন। হঠাৎ ডেকে বাজারে নিয়ে গিয়ে যেদিন দর্জির দোকানে জামা কাপড়ের মাপ নিতেন, যেদিন কাগজে মোড়া রঙিন স্যান্ডেলের প্যাকেটটা সামনে এনে খুলতেন, শীতকালে সকলের গায়ে পরা জাম্পারের ভিড়ে আমাদের জন্য এনে হাজির করতেন হাঁসের পালকের মতো নরম কার্ডিগেন, আমাদের তখন তাকে যাদুকর না ভেবে উপায় থাকতো না। পাড়ার ছেলেরা কোমরে রবার দেওয়া সিট কাপড়ের প্যান্ট পরতো, আব্বা আমাদের জন্য আনতেন চার পকেটওয়ালা ইংলিশ প্যান্ট। সেই প্যান্ট পরে আমাদের ডাঁট মেরে ঘুরে বেড়ানো দেখে ছেলে ছোকরার দলের হিংসা বা আফসোসের দৃষ্টিতে তাকানো চোখ এখনো জ্বলজ্বলে স্মৃতিতে। দিনের পর দিন বেতন না হওয়া মানুষটা তার ওই স্বল্প পয়সায় ঠিক কী করে আমাদের এত সব আবদার মেটাতেন একের পর এক, তা মাথায় ঢুকতো না কখনো।
আব্বা ছিলেন যেমন যাদুকর, তাঁর হাতের পরশেও ছিল তেমনই যাদু। আমরা আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করতাম, টুকটাক মাথা ব্যথা বা পেট ব্যথায় মা সারা বেলা টেপাটেপি করেও যে রোগ সারতো না, আব্বা এসে একবার হাত বুলিয়ে দিলেই আমরা কেমন দিব্যি অর্ধেক সুস্থ হয়ে যেতাম। অন্তত আমার ক্ষেত্রে প্রায়ই এমন ঘটতো। এ নিয়ে মা’র আক্ষেপের শেষ ছিল না তখন। টুংটাং বেল বাজিয়ে সাইকেল নিয়ে আব্বা বাড়ির আঙিনায় ঢোকামাত্র মা অভিযোগ করতেন, ‘এই নাও! তোমার ছেলের পেট ব্যথা! আমার ওষুধে তো কাজ হয় না। এইবার তুমি ঠিক করো।’
আব্বা সাইকেলটা বারান্দার খুঁটির সাথে ঠেস দিয়ে রেখে বাইরের জামা কাপড় না ছেড়েই তার শক্ত হাতে পেটের ওপর হাত বুলাতেন, কখনো চাপ দিতেন মৃদু, অমনি যেন একটু একটু করে পেটের ব্যথার কথা ভুলে যেতাম। কোলে করে তুলে নিয়ে খাওয়ার পাটিতে বসাতেন আব্বা। বলতেন, ‘হয়তো গ্যাস বেড়েছে! একটু ভাত খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।’ মা এসব গ্যাসট্যাসের কথা পাত্তা দিতেন না। কপট রাগতস্বরে বলতেন, ‘যে রোগের যে ওষুধ। বাপ বাড়ি এসেছে, এখন এমনি ঠিক হয়ে যাবে সব।’ অবাক হয়ে খেয়াল করতাম, আব্বা আসার পর সত্যি সত্যি ব্যথাট্যথা কোথায় উধাও হয়ে গেছে যেন সব।
জায়গা জমি ভাগাভাগি করার মতো আমাদেরকে নিয়ে একটা ভাগাভাগি হয়েছিল আব্বা আর মা’র মধ্যে, মনে পড়ে। অপেক্ষাকৃত শান্তশিষ্ট ও অনুগত স্বভাবের বড়ভাই ছিল মা’র ভাগে, আর বেয়ারা গোছের, নাওয়া-খাওয়া সব কিছু নিয়ে পিটপিট করা আমি ছিলাম আব্বার।
মা’র এ ভাগাভাগির কারণও ছিল অবশ্য। শতভাগ বাপ ন্যাওটা বলে যা বোঝায়, ছোটবেলায় আমি ছিলাম তাই। আমাকে বাড়িতে রেখে দুই একদিনের জন্যও কোথাও যাওয়া আব্বার পক্ষে ছিল প্রায় অসম্ভব। ফোর ফাইভে ওঠার আগ পর্যন্তও কোথাও কোনো অনুষ্ঠানে, দাওয়াতে-নিমন্ত্রণে গেলে আমি জোঁকের মতো লেগে থাকতাম তাঁর সাথে। কদাচিৎ বাধ্য হয়ে ছেড়ে গেলে তা নিয়ে সপ্তাহ দুই সপ্তাহ গাল ফুলিয়ে থাকতাম। মা বলতেন, ‘তোমার ছেলেকে নিয়ে তুমি যা খুশি তাই করো। যেখানে খুশি নিয়ে যাও, মাছ-গোস্ত খাওয়াও, না হয় পাঞ্জাবির পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াও, আমি তার ধার ধারি না। আমার ছেলেকে নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নাই। তাকে ডাল, ভর্তা, শাকপাতা যা দিই, তাই সই। সব সমস্যা তোমার, আর তোমার ছেলের।
মা’র কথা শুনে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে আব্বা বলতেন, ‘আমার আবার কী সমস্যা?’ আব্বার হাসি দেখে মা’র গলার ঝাঁঝ বেড়ে যেতো এবার আরো- ‘সমস্যা তো তোমারই! তুমিই তো লাই দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে এমন বানাইছো!’
আব্বার সাথে মা’র সেই ঝগড়া এখনো চালু আছে। এখনো সবকিছুতে আব্বাকেই দায়ী করেন তিনি। যদিও ঝগড়ার ধরন কিছুটা বদলেছে ইদানীং। আগে যেখানে আমাকে আব্বার ভাগে ঠেলে দিতেন মা, এখন আর দেন না তেমন। এখন বরং আমাদের চার ভাইকে নিজের সম্পত্তি মনে করে আব্বার সাথে রাগারাগি করেন নতুন অভিযোগে- ‘তখন কত করে বললাম এগুলোকে লেখাপড়া করানোর দরকার নাই। এই লোকটা শুনলো আমার কথা? শুনলো না। সবকটাকে পাঠালো বাইরে! এখন আর কেউ বাড়িতে থাকে না। লেখাপড়া না শিখিয়ে ছোটবেলায় ভ্যান কিনে দিলে ভালো হতো। অমুকের ছেলেরা সবাই ভ্যান চালায়ে খায়, তবুও সবাই বাড়িতে থাকে। বাপ-মার সামনে থাকে। আর আমার কোল যে খালি, সেই খালি-ই! আমার যে কাপাসির কান্দন, সেই কান্দনই! এই লোকটাই সব নষ্টের গোঁড়া।
নষ্টের গোঁড়া আব্বা মার কথা শুনে এখনো হাসেন। সেই হাসির আড়ালেই হয়তো লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন ছেলেগুলো কাছে না থাকার কষ্ট। প্রাত্যহিক জীবনের জটিলতার কাছে অসহায় তিনি। মা বুঝতে না চাইলেও আব্বা ঠিকই বোঝেন, যে পথে বয়ে চলেছে জীবন, চাইলেও ঘরে থাকা সম্ভব নয় তার ছেলেদের আর। মাঝেমাঝেই ফোন করে অবুঝ শিশুর মতো তিনি জিজ্ঞেস করেন, ‘অফিস ছুটি হবে কবে আব্বা? গাছের আমগুলো তো সব পেকে গেল! লিচুগুলো সব খেয়ে যাচ্ছে বাঁদুরের ঝাঁক-কাঠবিড়ালির দল!’
আব্বার নরম-শান্ত কণ্ঠের জিজ্ঞাসার মুখে শিগগিরই আসব বলে তাড়াতাড়ি ফোন রাখি। অথচ জানি সহসাই যাওয়া হচ্ছে না। যাওয়ার উপায় নেই! ইট পাথরের এ নগর জীবন, এ জীবনের নানাবিধ ব্যস্ততা সাঁড়াশীর মতো চেপে ধরে রাখে আমাকে, আমাদেরকে, সবাইকে। প্রবল ইচ্ছে থাকার পরও হয়ে ওঠে না! ডানা বেঁধে ছেড়ে দেওয়া পাখির মতো ভেতরটা ছটফট করলেও বছরে দুই তিন বারের বেশি পা দিতে পারি না বাড়ির উঠান-আঙিনায়। ব্যস্ততা আমাদের দেয় না অবসর। অথচ বুঝি, বাড়ির আঙিনার গাছগুলোর বয়স বেড়ে যাচ্ছে, সেইসাথে বয়স বেড়ে যাচ্ছে মা’র-আব্বারও। শতবর্ষী গাছের মতোই ডাল পালায়, গোঁড়ায়, কাণ্ডে শ্যাওলা জমে যাচ্ছে। তবুও অন্তর শীতল করা প্রশান্তির ছায়া হয়ে মাথার ওপর তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন এখনো আমাদের। সে ছায়ার নিচেই মাঝে মাঝে জিরিয়ে আসি আমরা। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে আবার ফিরে আসি এই নগর-জঞ্জালে।
ভালো থাকুক আমাদের সহ পৃথিবীর সকলের মাথার ওপর আশ্রয় হয়ে থাকা পিতা-মাতা গাছেরা। শতায়ু, শতবর্ষী হোক সবাই।